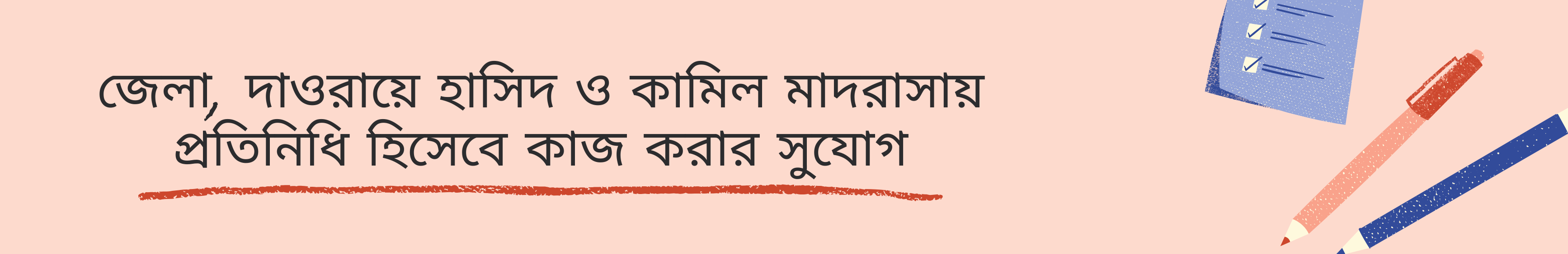কওমি কণ্ঠ ডেস্ক :
বাংলাদেশে চিকিৎসা খাতকে ঘিরে সবচেয়ে আলোচিত ও স্পর্শকাতর বিষয়গুলোর মধ্যে একটি হলো চিকিৎসকদের ভিজিট বা পরামর্শ ফি। সম্প্রতি রাজধানীসহ সারা দেশে এই ফি ক্রমাগত বাড়তে থাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। এর মধ্যে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে রিপোর্ট দেখাতে আবারও ভিজিট নেওয়া প্রসঙ্গে।
দ্বিতীয় এই ভিজিটের পক্ষে নানা যুক্তির পাশাপাশি সমালোচনা আসছে স্বয়ং চিকিৎসক সমাজ থেকেই। তারা বলছেন, সেবার ব্রত নিয়ে পেশায় আসার পর কিছু ব্যক্তি টাকার মেশিনে পরিণত হয়েছেন। তবে চিকিৎসকদের একটি বড় অংশই মনে করেন, ‘আধুনিক চিকিৎসা, সময়, শ্রম এবং পেশাগত মর্যাদার কথা বিবেচনা করলে ফি একেবারেই অযৌক্তিক নয়’।
রোগী ও চিকিৎসকদের মধ্যে এই ‘রিপোর্ট ভিজিট’ ইস্যু এক জটিল দ্বন্দ্বের জন্ম দিয়েছে। রোগীরা মনে করছেন চিকিৎসকরা সেবার নামে ব্যবসা করছেন, আর চিকিৎসকরা বলছেন তারা ন্যায্য পারিশ্রমিক নিচ্ছেন। এই দ্বন্দ্বের বোঝা গুনতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এক রোগের জন্য চিকিৎসা নিতে গিয়ে একজন রোগীকে দুবার ভিজিট দেওয়াকে তারা ‘মরার ওপর খাঁড়ার ঘা’ বলছেন।
স্বাস্থ্য খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ‘রিপোর্ট ভিজিট’ এখন চিকিৎসক সমাজের নৈতিকতা ও স্বাস্থ্য খাতের স্বচ্ছতার জন্য একটি বড় প্রশ্ন। যদি এখনই কোনো নীতিমালা প্রণয়ন না হয়, তবে ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যসেবায় আস্থার এই সংকট আরও গভীর হবে।
রাজধানীর স্কয়ার, ল্যাবএইডসহ বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে দেখা গেছে, প্রথমবার ডাক্তার দেখাতে রোগীরা এক থেকে দুই হাজার টাকা পর্যন্ত ভিজিট দিচ্ছেন। কিন্তু পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে নিয়ে চিকিৎসককে দেখাতে গেলে তাদের আবারও ভিজিট দিতে হচ্ছে কখনও ৪০০–৫০০ টাকা, আবার অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম ভিজিটের সমান টাকা। এতে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে, চিকিৎসক সমাজের নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে এবং নীতিনির্ধারকদের দিকেও আঙুল উঠছে।
ঢাকার একটি বেসরকারি টেলিভিশনে কাজ করেন কেফায়েত শাকিল। সম্প্রতি তিনি পরিবারের সদস্যকে নিয়ে বাংলাদেশ ফার্টিলিটি হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে গিয়ে ‘ডাবল ভিজিট’-এর অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তিনি জানান, প্রথমবার তিনি এক হাজার টাকা ভিজিট দেন। কিন্তু পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে নিয়ে আবার গেলে তাকে জানানো হয়, আবারও এক হাজার টাকা দিতে হবে।
শাকিল ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘প্রথম ভিজিটে তো পুরো চিকিৎসা হয়নি, কেবল টেস্ট করতে দিলেন। রিপোর্ট নিয়ে এলে আবার ফুল ভিজিট চাইলেন। এটি একেবারেই অমানবিক মনে হয়েছে, তাই না দেখিয়েই চলে এলাম।’
শুধু শাকিল নন, পপুলার হাসপাতালে মোহাম্মদপুর থেকে সেবা নিতে আসা মোহাম্মদ হোসেন এবং ল্যাবএইড হাসপাতালে গুলশান থেকে চিকিৎসা নিতে আসা শিক্ষক আজিজুল হকও একই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন। মোহাম্মদ হোসেন বলেন, ‘আমার মায়ের দীর্ঘমেয়াদি রক্তচাপের সমস্যা রয়েছে। প্রতি মাসে অন্তত দুবার তাকে ডাক্তার দেখাতে হয়। প্রথমবার ভিজিট এক হাজার টাকা, আর রিপোর্ট দেখানোর জন্য আবার ৫০০ টাকা। কখনও কখনও ডাক্তার প্রথম দিন পুরো ইতিহাস না নিয়ে দ্রুত প্রেশার (রক্তচাপ) মেপে রোগীকে ছেড়ে দেন। এরপর রিপোর্ট আসার পরই দ্বিতীয়বার ডাক্তারকে দেখাতে হয়। এটি আমাদের নিয়মিত রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সবমিলিয়ে দেখছি, রোগীরা এখন ব্যবসার পণ্য হয়ে উঠেছে।’
আজিজুল হক বলেন, ‘বেসরকারি হাসপাতালের ফি (ভিজিট) গড়ে ৭০০ থেকে ১৫০০ টাকা। আবার রিপোর্ট দেখাতে আলাদা ফি। আমাদের দেশে বিশেষ করে দরিদ্র পরিবারগুলো তাদের সন্তানদের চিকিৎসার জন্য ঋণ নিতে বাধ্য হচ্ছে। কখনও কখনও মনে হয় চিকিৎসা নয়, রোগীরা যেন ব্যবসার অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ডাক্তাররা বলবেন, আমাদের পেশাগত মর্যাদা এবং সময়ের মূল্য আছে। কিন্তু রোগীর চোখে এটি একপ্রকার অন্যায় এবং বাড়তি বোঝা।’
সম্প্রতি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের সামনে একাই প্ল্যাকার্ড হাতে দাঁড়িয়ে রিপোর্ট দেখানোর জন্য দ্বিতীয়বার ভিজিট/ফি নেওয়ার প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান কায়সার আলী। তিনি বলেন, ‘আমাদের হেলথ সেক্টরে দীর্ঘদিন ধরেই সাধারণ মানুষের জন্য নানা সমস্যা ও ভোগান্তি তৈরি হচ্ছে। একসময় ডাক্তার দেখার ফি ছিল ২০০ থেকে সর্বোচ্চ ৫০০ টাকা। কিন্তু আজকাল সেটি ছাড়িয়ে এক হাজার, এমনকি কোনো কোনো ডাক্তার দুই হাজার টাকা পর্যন্ত ভিজিট নিচ্ছেন। শুধু মূল ভিজিটই নয়, রিপোর্ট দেখার জন্য অতিরিক্ত ৫০০-৬০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। কেউ কেউ এক হাজার টাকা পর্যন্ত নিচ্ছেন।’
‘আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ (পৌনে পাঁচ কোটি মানুষ) এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছেন। এই অবস্থা থেকে রোগীদের জন্য চিকিৎসা নেওয়া স্বাভাবিকভাবেই কঠিন। এমন পরিস্থিতিতে যদি প্রথমবার মোটা অঙ্কের ভিজিট দিয়ে পরের দিন আবার রিপোর্ট দেখানোর জন্য নতুন ভিজিট দিতে হয়, তাহলে এটি স্পষ্টতই একটি অনৈতিক চর্চা। যদিও ডাক্তাররা বলবেন, তারা দীর্ঘদিন পড়াশোনা ও প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, তাই এই অর্থ নেওয়া জাস্টিফাইড (ন্যায্য)।’
তার অভিযোগ, ‘দুবার ফি নেওয়ার অর্থ হলো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও আলাদা পার্সেন্টেজ পাচ্ছে। অর্থাৎ রোগীরা হয়ে উঠেছে একপ্রকার ব্যবসার পণ্য। এমন প্র্যাকটিস আগে বাংলাদেশে ছিল না, কিন্তু এখন তা নিয়ম এবং চিকিৎসকদের অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।’
রাজধানীর ল্যাবএইড হসপিটালে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করছেন এমন একজন অধ্যাপক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘রিপোর্ট দেখার জন্য বর্তমানে প্রায় সব ডাক্তার আলাদাভাবে ভিজিট নেন। তবে, অধিকাংশ চিকিৎসক রিপোর্ট দেখানোর ফি সাধ্যের মধ্যে রাখেন। কিন্তু কিছু ডাক্তার আছেন যারা রোগী দেখার সময় মোটা অঙ্কের ভিজিট নেওয়ার পরও রিপোর্ট দেখতে ফুল ভিজিট নেন। এটি রোগীর ওপর জুলুমের সমতুল্য।’
‘আমি নিজেও রিপোর্ট দেখার জন্য আলাদা ফি নিই। সেটি ৩০০ টাকার বেশি নয়। রোগীর সমস্যার প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে কখনও ফি নিই না। ব্যক্তিগতভাবে আমি এটির বিপক্ষে, খুব খারাপ লাগে। অথচ কারও কারও কাছে এটি স্বাভাবিক নিয়মে দাঁড়িয়েছে। বিষয়টি আমাদের সমাজের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগের।’
তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, ‘পপুলার হাসপাতালগুলো যেমন ল্যাবএইড বা ইবনে সিনা— সেখানে ভিজিট মোটামুটি সাধ্যের মধ্যে। কিন্তু স্কয়ার, ইউনাইটেড বা এভারকেয়ার লেভেলের হাসপাতালগুলোতে ভিজিট অনেক বেশি। এখানে সমস্যা হলো, প্রথমেই মোটা অঙ্কের ভিজিট নেওয়া হয়ে গেছে, তারপর রিপোর্ট দেখার জন্য আবার পুরো ভিজিট নেওয়া হয়। এটি স্পষ্টভাবে অন্যায়। এমন পরিস্থিতিতে সরকার একটি নীতিমালা বা বাধ্যবাধকতা আনার মাধ্যমে এই বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।’
বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ডা. মো. শামীম আহমেদ বলেন, ‘যতটুকু জানি, পরীক্ষার রিপোর্ট দেখতে চিকিৎসকরা সাধারণত ২০০–৩০০ টাকা নেন। এটি যৌক্তিক। তবে, কেউ যদি রিপোর্ট দেখার জন্য আবার পুরো ভিজিট নেন, তা অত্যন্ত অন্যায়। এমনকি হাফ ভিজিট নেওয়াও উচিত নয়। যদি আলাদা ফি নিতে হয়, সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২০০–৩০০ টাকার বেশি হওয়া উচিত নয়। কারণ, রোগীকে সঠিক চিকিৎসা দিতে গেলে রিপোর্টগুলো সময় নিয়ে দেখা এবং বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, যা আলাদা সময় দাবি করে।’
‘দ্বিতীয়বার ভিজিটের প্রচলন পাঁচ বছর আগেও এতটা ছিল না। এখন এটি অনেক চিকিৎসকের কাছে নিয়মে পরিণত হয়েছে। অসংখ্য মানুষ তাদের ভিটেমাটি বিক্রি করে চিকিৎসা করাচ্ছেন। সেই পরিস্থিতিতে আমাদের সদয় হওয়া উচিত। আমরা এই পেশায় এসেছি মানুষকে সেবা দিতে, নীতি-নৈতিকতা ভুলে যাওয়া উচিত নয়। আমরা ভেবেছিলাম ৫ আগস্টের পর স্বাস্থ্যসেবায় পরিবর্তন আসবে, সবকিছু নিয়মে আসবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।’
স্বাস্থ্য অর্থনীতিবিদরা বলছেন, বাংলাদেশে ভিজিট/ফি একেবারেই নিয়ন্ত্রণহীন। ইউরোপ বা আমেরিকার মতো দেশে এটি নির্ধারিত থাকে বীমা সিস্টেমের মাধ্যমে। বাংলাদেশে বীমা কাভারেজ না থাকায় পুরো খরচ বহন করতে হয় রোগীদের। ফলে চিকিৎসা নিতে গিয়ে নিঃস্ব হচ্ছে অসংখ্য পরিবার। বিশ্বব্যাংকের ২০২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে মোট স্বাস্থ্যব্যয়ের ২৮.৫২ শতাংশ রোগীর পকেট থেকে খরচ হয়। এটি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।
সম্প্রতি একটি গবেষণায় দেখা গেছে, উচ্চ রক্তচাপের রোগীদের মধ্যে ২৬ শতাংশ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা নিতে পারছেন না। এছাড়া, চিকিৎসার বাড়তি ব্যয়ের কারণে ৪৬ শতাংশ রোগী অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছেন। তাদের মধ্যে ১০ শতাংশ বা তার চেয়ে বেশি মানুষ আয়ের পুরোটাই ব্যয় করেছেন চিকিৎসায়। বর্তমানে ক্যানসার সবচেয়ে ব্যয়বহুল চিকিৎসা। দীর্ঘমেয়াদি এই চিকিৎসায় রোগীদের প্রায় ৬৮ শতাংশ ওষুধে এবং ১২ শতাংশ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যয় হয়। ফলে প্রতি বছর প্রায় ৫০ লাখ মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যাচ্ছেন।
ঢাকার এক জরিপে দেখা গেছে, দরিদ্র পরিবারগুলোর মাসিক গড় আয় নয় হাজার ৮৫২ টাকা। অথচ তাদের চিকিৎসার জন্য গড় ব্যয় হয় তিন হাজার ২২৬ টাকা, অর্থাৎ আয়ের প্রায় ৩৩ শতাংশ। বাড়তি এই ব্যয়ের কারণে অনেক রোগী সময়মতো চিকিৎসা নিতে পারছেন না বা দেরিতে চিকিৎসা শুরু করছেন। বিশেষ করে উচ্চ ভিজিট এবং ডাবল ভিজিট প্রথার কারণে সাধারণ মানুষ হাসপাতালে যাওয়ার আগে দ্বিধায় পড়ছেন বলে গবেষণাগুলোতে উঠে এসেছে।
এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের এক গবেষক নাম প্রকাশ না করে বলেন, ‘বেসরকারি চিকিৎসা খাত এখন বাজারের নিয়মে চলছে। এখানে কোনো নীতিমালা নেই। ফলে ডাক্তাররা নিজের ইচ্ছামতো ভিজিট নিচ্ছেন। এতে সাধারণ মানুষের ওপর আর্থিক চাপ বেড়েই চলেছে।’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. সৈয়দ আব্দুল হামিদ একটি গবেষণা প্রতিবেদনে জানিয়েছেন, একজন সাধারণ ব্যক্তি স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে বছরে যদি ১০০ টাকা খরচ করেন, তার মধ্যে প্রায় ৬৪ টাকা চলে যায় ওষুধ কেনার জন্য। অর্থাৎ, ব্যক্তির সিংহভাগ আয় ওষুধের পেছনে ব্যয় হচ্ছে।
তিনি আরও বলেন, দেশের ৮৬ শতাংশ মানুষ চিকিৎসা গ্রহণ করেন বেসরকারি খাত থেকে। আর মাত্র ১৪.৪১ শতাংশ মানুষ সরকারি হাসপাতালে সেবা নিচ্ছেন। ফলে চিকিৎসা খরচের ভারে প্রতি বছর ৮৬ লাখের বেশি মানুষের আর্থিক অবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিষয়টি আরও গুরুতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে, যখন উচ্চ ব্যয়ের কারণে প্রায় ১৬ শতাংশ মানুষ স্বাস্থ্যসেবা নেওয়া থেকে বিরত থাকছেন। অর্থাৎ প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তিন কোটির বেশি মানুষ হাসপাতালে বা চিকিৎসকের কাছে যাচ্ছেন না। এই পরিস্থিতি মূলত সরকারিভাবে মানসম্মত সেবার অভাবে তৈরি হচ্ছে। মানুষ বাধ্য হচ্ছেন বেসরকারি সেবা গ্রহণ করতে।
উত্তরণের উপায় নিয়ে অধ্যাপক হামিদ বলেন, ‘সরকারি স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা পূর্ণমাত্রায় সচল করতে হবে। হাসপাতালে পর্যাপ্ত চিকিৎসক, নার্স, ডায়াগনস্টিক ব্যবস্থা ও ওষুধ নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া, চিকিৎসকদের বেসরকারি প্র্যাকটিস সীমিত করে হাসপাতালের ভেতরে অর্থের বিনিময়ে রোগী দেখার ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। এতে হাসপাতালের আয় বাড়বে, চিকিৎসকও সঠিক অর্থ পাবেন। রোগীদের অযাচিত ব্যয়ও কমবে।’
রিপোর্ট দেখাতে গিয়ে দ্বিতীয় ভিজিট প্রসঙ্গে সরাসরি মন্তব্য না করলেও পুরো কনসালট্যান্ট ভিজিটে ‘ভারসাম্য আনা জরুরি’ বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায়) অধ্যাপক মো. সায়েদুর রহমান। বলেন, ‘চিকিৎসকদের ফি-সংক্রান্ত আলোচনা অত্যন্ত সংবেদনশীল। কারণ, এটি রোগী ও চিকিৎসকের মধ্যে ন্যায্যতার প্রশ্ন তোলে।’
তার মতে, ‘প্রফেশনাল ফি কি বাংলাদেশে নির্ধারণযোগ্য, তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। স্বাস্থ্যসেবা সংবেদনশীল একটি সেবা। ঠিক যেমন একজন উকিল বা আর্কিটেক্টের ফি সংবেদনশীল। এখানে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, যাদের ওপর ফি প্রয়োগ করা হবে তাদের সম্মতি থাকা উচিত। অন্যথায় দুই পক্ষের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করা কঠিন হবে। একজন প্রোভাইডার সন্তুষ্ট থাকবেন, কিন্তু রোগীকে এফোরডেবল (সাশ্রয়ী মূল্য) সেবা দেওয়া হবে কি না, সেটি নিশ্চিত করতে হবে। আইন, নীতি-নৈতিকতা ও প্রফেশনাল লিগ্যালের মধ্যে ব্যালান্স থাকা জরুরি।’
তিনি বিশেষভাবে ‘রেফারেল সিস্টেম’-এর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এটি এমন একটি পদ্ধতি যেখানে একজন ব্যক্তি বা সেবাদানকারী অন্য কাউকে আরও উন্নত বা নির্দিষ্ট সহায়তা, তথ্য বা বিশেষজ্ঞ সেবার জন্য অন্য কোনো উপযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে পাঠান। বলেন, ‘ধরা যাক, আপনি পেপটিক আলসারের জন্য সরাসরি একজন গ্যাস্ট্রোএন্ট্রোলজিস্টের কাছে গেলেন। সেখানে ফি অনেক বেশি হবে। কিন্তু সঠিক রেফারেল সিস্টেম থাকলে প্রথমে রোগী ২০০–৩০০ টাকার ফি দিয়ে জেনারেল প্র্যাকটিশনার দেখাতেন, তারপর প্রয়োজন হলে বিশেষজ্ঞের কাছে রেফার করা হতো। এতে রোগীর অযাচিত খরচ অনেকাংশে কমত এবং প্রাপ্য চিকিৎসা ঠিকভাবে দেওয়া সম্ভব হতো।’
তিনি আরও উদাহরণ টেনে বলেন, ‘অনেক দেশের চিকিৎসকেরা স্টপওয়াচ ব্যবহার করেন। রোগী প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে টাইমিং শুরু হয়, প্রেসক্রিপশন দেওয়ার পর স্টপওয়াচ বন্ধ হয় এবং রোগী বুঝতে পারেন কত টাকা বিল হয়েছে। শর্ট ভিজিট, মিডিয়াম ভিজিট ও লং ভিজিট— সব ধরনের ভিজিট নির্ধারণ করা যায়। এটি রোগী ও চিকিৎসক— উভয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে।’
অধ্যাপক সায়েদুর রহমান মনে করিয়ে দেন, ‘এই পদ্ধতিকে অবশ্যই সাংস্কৃতিক ও পেশাগতভাবে মানিয়ে নিতে হবে। শুধুমাত্র প্রযুক্তি নয়, সামাজিক ও পেশাগত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো জরুরি। এতে রোগীর আর্থিক বোঝা কমবে, চিকিৎসার মান বজায় থাকবে এবং চিকিৎসক ও হাসপাতাল উভয়ই ন্যায্যভাবে সেবা দিতে পারবে।’
(মূল রিপোর্ট : ঢাকা পোস্ট)
.png)